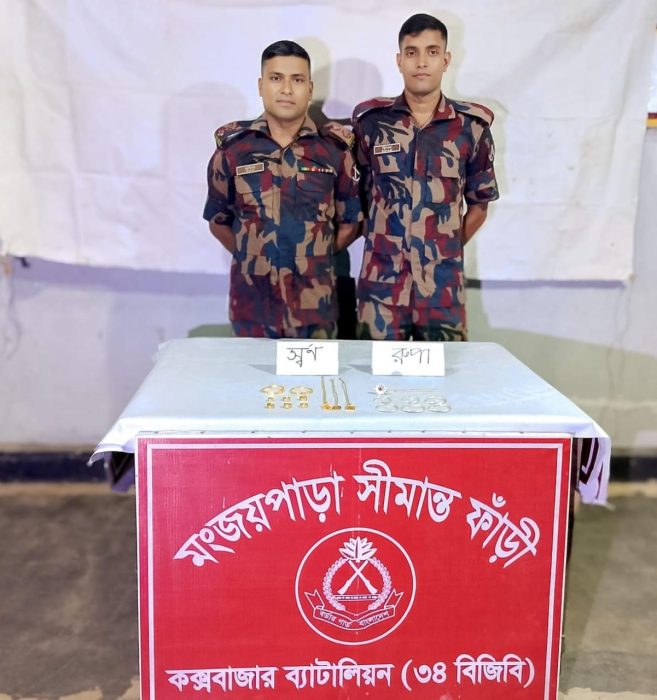এশিয়ার মূল্যবান বিরল খনিজ টার্গেট করল যুক্তরাষ্ট্র!


একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন এক পরিভাষা জায়গা করে নিয়েছে—‘বিরল খনিজ কূটনীতি’ বা রেয়ার আর্থ ডিপ্লোমেসি। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই এটি এখন বৈশ্বিক শক্তির নতুন মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।
একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন এক পরিভাষা জায়গা করে নিয়েছে—‘বিরল খনিজ কূটনীতি’ বা রেয়ার আর্থ ডিপ্লোমেসি। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই এটি এখন বৈশ্বিক শক্তির নতুন মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতার প্রায় প্রতিটি প্রযুক্তির মেরুদণ্ডে থাকা ১৭টি বিরল খনিজ উপাদানকে ঘিরেই এ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে।
এশিয়ার পাহাড়ঘেরা ভূভাগ ও নদীনির্ভর অরণ্যের মাটির গভীরেও লুকিয়ে আছে এ বিরল সম্পদ। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর অব্যবহৃত বিরল খনিজ মজুদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতেই রয়েছে, যা ভবিষ্যতের শক্তি রূপান্তর ও প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য এক বিশাল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এ বিরল খনিজ বর্তমানে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
রসায়নবিজ্ঞানের পর্যায় সারণির ল্যান্থানাম থেকে লুটেটিয়াম—এ ১৫ ‘ল্যান্থানাইডের’ সঙ্গে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়াম মিলিয়ে মোট ১৭টি উপাদানকে বলা হয় বিরল খনিজ। প্রায়ই একই খনিজ ভূমিতে পাশাপাশি থাকে; আলাদা করতে হয় সূক্ষ্ম রসায়ন আর ধৈর্যের কারিগরি দিয়ে। ফাইটার জেট, সাবমেরিন সেন্সর, রাডার, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিকাঠামো, স্মার্টফোনের খুদে স্পিকার, বৈদ্যুতিক গাড়ির শক্তিশালী মোটর, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, উইন্ড টারবাইনের জেনারেটর সবখানেই এগুলোর ব্যবহার অপরিহার্য। ল্যাপটপ, টেলিযোগাযোগ যন্ত্র, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার চিপ থেকে শুরু করে চিকিৎসা ইমেজিং ও ডায়াগনস্টিক যন্ত্র—সবখানেই এর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে আধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এ উপাদানগুলোর ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো দেশগুলো এগুলোকে ‘কৌশলগত উপাদান’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। টেসলা, বিএমডব্লিউ, টয়োটা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রায় সব ইভি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই এ উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের জনপ্রিয়তা এ চাহিদাকে আগামী দশকেও বহুগুণ বাড়াবে। ফলে এ উপাদানগুলো এখন কেবল শিল্প কাঁচামাল নয়, বরং শক্তির নতুন ভূরাজনীতি গড়ে তোলার হাতিয়ার হয়ে উঠছে। কারণ এগুলোর নিয়ন্ত্রণ মানেই আধুনিক প্রযুক্তি, সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণ। চীন কয়েক দশক ধরে এ খাতে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছে; তাই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এখন বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে বিরল খনিজ নিয়ে প্রতিযোগিতা এখন শুধু বাণিজ্যের নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও শক্তির কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ও গোল্ডম্যান স্যাকস গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বিশ্বের মোট বিরল খনিজ মজুদের ২০ শতাংশেরও বেশি এ অঞ্চলে রয়েছে। চীন একাই বিশ্ব মজুদের ৪৯ শতাংশ এবং খননের প্রায় ৬৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রসেসিং বা পরিশোধনের হিসাব ধরা হলে সাপ্লাই চেইনের ৮৫-৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে চীন। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অজস্র অনাবিষ্কৃত খনি ছড়িয়ে আছে। ভিয়েতনামে রয়েছে প্রায় ৩৫ লাখ টন রিজার্ভ, আর মিয়ানমার একাই ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ চীনে রফতানি করেছে। এ বাজারে চীনের একচেটিয়া প্রভাব ভাঙতেই এখন যুক্তরাষ্ট্র নতুন কৌশল নিয়েছে।
এরই মধ্যে মিয়ানমার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের আভাস মিলছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিরল খনিজ ঘিরে নতুন ভূরাজনৈতিক কৌশল। মিয়ানমারের কাচিন রাজ্যে মজুদ বিরল খনিজের বড় অংশ বিদ্রোহী গোষ্ঠী কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি মিয়ানমার সরকার অথবা বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করে এসব বিরল খনিজের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরিকল্পনা করছে। সম্প্রতি যুদ্ধবিধ্বস্ত এসব অঞ্চল সফরও করেছেন মিয়ানমারে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। প্রসঙ্গত, মিয়ানমারের মাটিতে পাওয়া ডিসপ্রোসিয়াম, টার্বিয়াম ও ইট্রিয়ামের মতো খনিজ বিশ্ববাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেভি রেয়ার আর্থ উপাদান; যা সামরিক সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক গাড়ি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য অপরিহার্য।
চ্যাথাম হাউজের এশিয়া-প্যাসিফিক প্রোগ্রামের গবেষক উইলিয়াম ম্যাথিউজের মতে, ‘খাতটি চীনকে এমন এক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দিয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের জন্য অপরিহার্য বিভিন্ন সাপ্লাই চেইনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে—সেমিকন্ডাক্টর থেকে শুরু করে বিমান উৎপাদন পর্যন্ত। এ সাপ্লাই চেইনে চীনের প্রভাব কমাতে যুক্তরাষ্ট্র নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে।’ চ্যাথাম হাউজেরই আরেক গবেষক প্যাট্রিক শ্রোডারের মতে, ‘অসংখ্য হাই-টেক শিল্প রেয়ার আর্থ ছাড়া কার্যত কিছুই তৈরি করতে পারে না। চীন বাজার দখল করেছে, কারণ এ উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দূষণকারী ও ধ্বংসাত্মক। অন্য দেশগুলোর কাছে তখন মনে হয়েছিল, সেই দূষণটা চীনের ওপর থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সে সময় শেষ। এখন ভূরাজনীতি বাণিজ্যের স্থিতাবস্থা বদলে দিয়েছে।’
গত সপ্তাহে আসিয়ান সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাসিমুখে হাজির হলেও পর্দার আড়ালে তিনি বিরল খনিজ ঘিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলোর ওপর চাপ বাড়ান। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষর করেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক; যার মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে দেয়া হয়েছে নতুন খনিজ মজুদের ওপর অগ্রাধিকারমূলক বিনিয়োগ ও ক্রয়াধিকার। মালয়েশিয়ার চুক্তিতে যুক্ত করা হয়েছে এমন ধারা, যা ভবিষ্যতে দেশটির কাঁচা খনিজ রফতানিতে কোনো কোটা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপে বাধা দেবে।
ইন্দোনেশিয়া ও লাওস এরই মধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করছে খনিজ খাতের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য। ইন্দোনেশিয়ায় গঠন হয়েছে একটি পৃথক খনিজ মন্ত্রণালয়ও। মালয়েশিয়া একদিকে জাতীয় বন সংরক্ষণের আওতায় থাকা অঞ্চলগুলোতে খনন নিষিদ্ধ রাখলেও অন্যদিকে ১ লাখ ৪৪ হাজার হেক্টর অরণ্যের বাইরে নতুন খনন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। পাহাংয়ের ১৪০ হেক্টরজুড়ে লিনাস কারখানাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র রেয়ার আর্থ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, যা এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার আকরিকই প্রক্রিয়াজাত করে।
ভারতের ক্ষেত্রেও ওয়াশিংটন যৌথ অনুসন্ধান ও রিসাইক্লিং প্রযুক্তি উন্নয়নে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে, আর ভিয়েতনামকে নতুন সরবরাহ শৃঙ্খলের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এ ধারাবাহিক তৎপরতা স্পষ্ট করে, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের প্রভাববলয় থেকে বিরল খনিজ সরবরাহকে মুক্ত করতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি নতুন খনিজ কূটনীতি গড়ে তুলছে।
মার্কিন নীতি-গবেষণা প্রতিষ্ঠান শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ফেলো কার্ল ফ্রিডহফের ভাষায়, ‘৫০টির বেশি উপাদানকে “ক্রিটিক্যাল মিনারেল” হিসেবে চিহ্নিত করে ওয়াশিংটন নিরাপত্তা, ক্লিন-এনার্জি ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জোগান সুরক্ষায় অংশীদারত্ব, বিনিয়োগ ও নীতিপ্রণোদনা বাড়াচ্ছে। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ হলো চীনের নিয়ন্ত্রিত প্রসেসিং চেইন ভেদ করে স্কেলে রিফাইনিং ক্ষমতা দাঁড় করানো। তাই মার্কিন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বিরল খনিজের জন্য নতুন অংশীদার খোঁজা এবং সে দেশগুলোকে কেন্দ্র করে হাব গড়ে তোলা, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তর।’