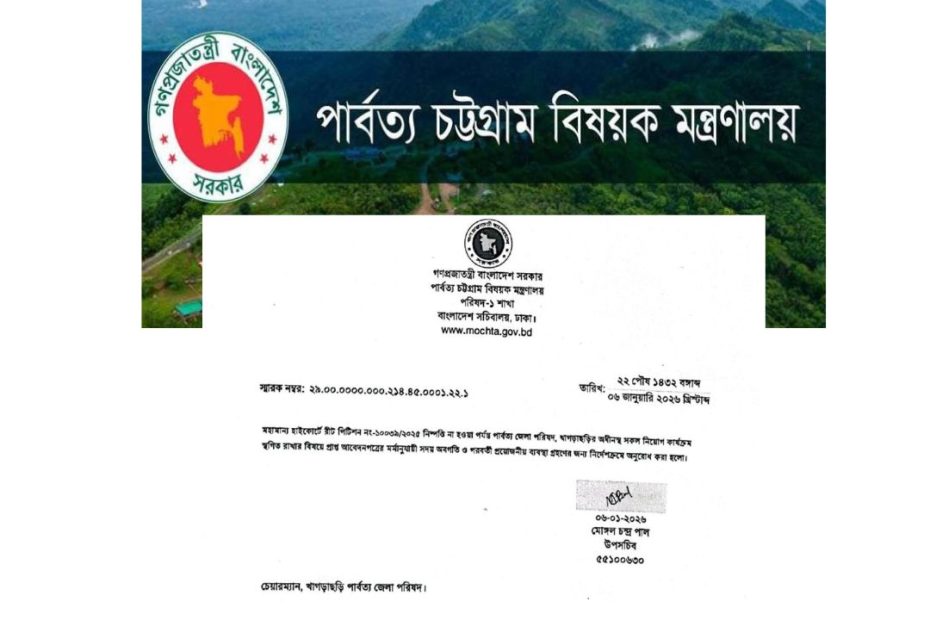ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ গঠনে ভাষার ভূমিকা অপরিহার্য


সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে মোট ৫১ টি নৃগোষ্ঠীর বসবাস। তার মধ্যে বাঙালিরা বৃহৎ নৃ- গোষ্ঠী, এবং জনসংখ্যা বিচারের ৫০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। এই ৫১ টি নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে আবার ৪১ টি ভাষাভাষী গোষ্ঠী রয়েছে। তবে এই সংখ্যা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। কেননা এখানে অনেক নাম রযেছে যাদেরকে পৃথক জাতি গোষ্ঠী না বলে হয়তো পৃথক সম্প্রদায় বা বংশ-গোষ্ঠী বলা যেতে পারে, কিংবা এই ৪১ টি ভাষার সবগুলোই স্বতন্ত্র ভাষার বৈশিষ্ট্য পেতে পারে কিনা, নাকি উপভাষা বলা হবে- এ নিয়ে অনেকের সংশয় রয়েছে। সেই বিতর্কে যেতে চাই না।
তবে এই ৫০ টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং ৪০ স্বতন্ত্র ভাষা বাংলাদেশের সম্পদ। বৈচিত্র্যময় জাতি ও বৈচিত্র্যময় ভাষা গোষ্ঠী সম্বলিত বাংলাদেশী জাতি, জাতি হিসেবে আমাদের গর্বিত করে। বাঙালি হিসেবে আমরা গর্ব অনুভব করি যে, এই দেশে আমাদের চল্লিশটি ভাষা এবং পঞ্চাশটি স্বতন্ত্র নৃ-গোষ্ঠী রযেছে। একটি জাতির উৎকর্ষতার জন্য এই বৈচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই আমরা দৃঢ়ভাবে এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও বৈচিত্র্যময় ভাষা সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য জাতি হিসেবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।
বলা হয়ে থাকে, কোন একটি জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চাইলে প্রথমে তার ভাষা ধ্বংস করে দাও। বিশেষ করে ভাষাভিত্তিক জাতি গোষ্ঠীর জন্য এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য। ভাষা ছাড়া এ ধরণের জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বই যেখানে হুমকির মুখে পড়ে, সেখানে ভবিষ্যৎ গঠনের প্রশ্ন অবান্তর। ভাষিক জাতীগোষ্ঠিগুলোর ভাষার সাথে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনপ্রণালি জড়িত থাকে। তার স্বপ্ন গড়ে ওঠে ভাষার মাধ্যমেই। ফলে ভাষিক জাতিগোষ্ঠির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। স্বতন্ত্র ভাষার সংরক্ষণ, প্রচার ও ব্যবহার ছাড়া কোন ভাষাভিত্তিক জাতি গোষ্ঠীর টিকে থাকতে পারে না। এটা বুঝতে পেরেই আমাদের পূর্বপুরুষ কোন ১৯৫২ সালে রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে ভাষার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। আজ সেই ত্যাগ ও ইতিহাস বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। জাতি হিসেবে মাতৃভাষা সংরক্ষণের এই অঙ্গীকার থেকে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বিশ্বের বুকে এটি একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের দায় ও দায়িত্ব কেবল বাংলা ভাষা নয় কিম্বা বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী সমূহের সকল ভাষা সংরক্ষণ, প্রচার ও ব্যবহার নিশ্চিত করা নয়। সারা বিশ্বের সকল মাতৃভাষা নিয়ে কাজ করাও এই প্রতিষ্ঠানের দায় ও দায়িত্ব। সে বিচারে এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বুকে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।
অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকার পরেও বাংলাদেশ থেকে একটি ভাষা (সৌরা ভাষা) বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও আরো চৌদ্দটি ভাষা প্রায় বিলুপ্তপ্রায়। এদের মধ্যে কোন কোন ভাষায় মাত্র কয়েকজন লোক কথা বলেন। তারা হারিয়ে গেলে এই ভাষাগুলো হারিয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং জাতি হিসেবে আমাদের জন্য খুবই লজ্জাকর। এ সকল বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিপুল দায় ও দায়িত্ব রয়েছে। আমরা মনে করি প্রতিষ্ঠানটি তার দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করবে না। মিডিয়া কর্মী হিসেবে আমরা এ ব্যাপারে আমাদের অংশে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
ভাষা বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ এর লিখিত রূপ না থাকা। বিশ্বে সকল ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বাংলাদেশে অবস্থিত একচল্লিশটি ভাষার মধ্যে মাত্র আটটি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। বাকি কিছু ভাষা রোমান ও বর্মী লিপি ব্যবহার করে নিজ ভাষার লিখিত রূপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আমার মতে, যে সমস্ত ভাষার এখনো কোন বর্ণমালা নেই সেই ভাষাগুলো উচ্চ বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রযেছে। আমি কোন ভাষা বিশেষজ্ঞ নই। তবে, একজন সংবাদ কর্মী ও গবেষক হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে প্রায় ৩০ বছর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবাদে আমার দেখা কিছু অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরতে চাই।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি তে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সব উদ্যোগই নেয়া হয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এর সাফল্য খুবই সামান্য। এর জন্য ভুলনীতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনাগ্রহই মূলত দায়ী। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করলেও সেখানকার বড় ও খ্যাতনামা স্কুলগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। এমনকি সরকারী নামকরা স্কুলগুলোতেও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দানের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। অভিভাবকদেরও এ নিয়ে চাহিদা বা দাবী নেই। পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর অগ্রসর অংশের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় না। তারা যেখানে তাদের সন্তানদের পড়াশোনা করায়, সেই সেই খ্যাতনামা বড় এবং শহুরে স্কুলগুলোতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই এবং এ নিয়ে তাদের মধ্যেও কোন দাবিও পরিলক্ষিত হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের অভিমত, প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ পরবর্তী মাধ্যমিক স্তরে যেহেতু বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুরা মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে বাংলায় পড়তে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ কারণে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা দানে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এটি অনেক সময় শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করছে। অনেক অভিভাবক যারা স্থানীয় ভাষায় শিশুকে পাঠদান করাতে অনাগ্রহী তারা কাছের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় ভাষায় পাঠদান করার ফলে সেখানে না পাঠিয়ে দূরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণ করতে পাঠায়। এই দূরত্ব, সময় ও যাতায়াতের ঝুঁকি অনেক সময় শিশুদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সেগুলো একেবারেই প্রান্তিক ও অনগ্রসর এলাকায় অবস্থিত। এখানে ভালো শিক্ষকের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি যোগ্য শিক্ষকগণ সেখানে থাকেন না। হয়তো অনেকেই জানেন না পাহাড়ে ‘বর্গা শিক্ষক’ নামে একটি সিস্টেম পরিচালিত রয়েছে। এই সিস্টেমে একজন সরকারি শিক্ষক তিনি যে এলাকায় পোস্টেড, সেখানে যান না এবং থাকেনও না। তিনি থাকেন শহরে। সেখানে প্রাইভেট পড়িযে বা অন্য কোন আর্থিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অধিক লাভবান হন। আর তার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় একজন ব্যক্তিকে ভাড়া করেন, যিনি একটি নিদিষ্ট টাকার বিনিময়ে উক্ত শিক্ষকের ক্লাসগুলোতে পাঠ দান করেন। তাদেরকেই মূলত ‘বর্গা শিক্ষক’ বলা হয়। বিষয়টি সকলের জানা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে বছরের পর বছর এভাবেই চলে আসছে।
অভিযোগ রয়েছে, অনেক শিক্ষক ক্লাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদানের সময় কথোপকথনে অন্য ভাষা ব্যবহার করেন। সে কারণে সরকারি উদ্যোগ ও বই পুস্তক থাকলেও স্থানীয় ভাষায় পাঠ গ্রহণে যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এছাড়াও পাশাপাশি পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বসবাসের ফলে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ছাত্রদের উপস্থিতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষাদানে অন্যতম প্রতিবন্ধক। উদাহরণ স্বরূপ, একটি চাকমা অধ্যুষিত এলাকার একটি স্কুলে কিছু মারমা ও ত্রিপুরা শিশু পড়াশোনা করে। ফলে একই ক্লাসে, একই সাথে তারা পাঠ গ্রহণ করে থাকে। সেখানে যখন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে একটি নিদিষ্ট ভাষায় পাঠদান চালু করা হয় তখন সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়। ফলে ওই স্কুলে পাঠ গ্রহণকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী বিপদে পড়েন। তখন বাধ্য হযে তারা স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য মতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সকল শিশুরা চাকমা ভাষায় পাঠ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট সুফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
অন্যদিকে বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা গ্রহণের মূল মাধ্যম কম্পিউটার, মোবাইল ও ইন্টারনেট। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এ সকল ভাষার বর্ণমালা গুলো ইন্টারনেটের ভাষায় পরিণত করতে না পারাটাও এই ভাষা সংরক্ষণের অন্যতম অন্তরায়। ইতোপূর্বে চাকমা ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষা হিসেবে চালু করার জন্য বিশাল একটি বাজেট দেয়া হলেও, সামান্য কিছু অগ্রগতি ছাড়া বাকিটা লুটপাটের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ভাষায় পরিণত করতে হলে স্বতন্ত্র কিবোর্ড প্রযোজন। যা আমরা প্রণয়ন করতে পারিনি।
উল্লিখিত আলোচনা সাপেক্ষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে আমার কতিপয় সুপারিশ:
১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা। যে সকল ভাষার বর্ণমালা রযেছে সে সকল ভাষার বর্ণমালা, উচ্চারণ এবং অভিধান প্রণয়ন।
২. যে সকল ভাষার লিখিত রূপ রয়েছে সে সকল ভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি, উপকথা পুস্তক আকারে প্রকাশের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা।
৩. যে সকল ভাষার বর্ণমালা নেই সেসকল ভাষা সংরক্ষণের জন্য এর লিখিত রূপ প্রণয়নকল্পে বাংলা বর্ণমালা প্রচলন করা। এতে দ্বিবিধ লাভ রয়েছে। প্রথমত, বাংলা ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা অধিক হওয়ায় অধিকাংশ সাউন্ড এই ভাষায় উচ্চারণ করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভাষী বর্ণমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এটা অনেকটা অপ্রযোজনীয় হয়ে পড়ে। সেগুলো শেখা ও পাঠদান করার ক্ষেত্রেও অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালায় উক্ত ভাষাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচার করা গেলে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা বর্ণমালা শেখা সহজ হওয়ার কারণে এই ভাষা শেখা ও পাঠদান করা যেমন সহজ হবে তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার যে অভিযোগ রয়েছে সেটাও দূরীভূত হবে। তবে সেটা অবশ্য কোনভাবেই চাপিয়ে দিয়ে নয়। উক্ত ভাষিক জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে এ কাজটি করা যেতে পারে। ইতোপূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্পেশাল এসিসট্যান্ট দায়িত্বে থাকাকালে চাকমা ভাষায় শিক্ষা ও বর্ণমালা এভাবে শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। তবে মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বাধায় সে উদ্যোগ সফল হয়নি। সেক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালা(ভাষা নয়) গ্রহণ একসাথে বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে সেজন্য উক্ত ভাষিক জনগোষ্ঠীর স্বতস্ফুর্ত সম্মতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাদের সম্মতির মাধ্যমেই এ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিকতার পাশাপাশি ঐচ্ছিকভাবেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিশেষ করে সহশিক্ষার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা শিখতে পারবে। এটি ঐচ্ছিক থাকবে। ফলে শহরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষাদান করে না, তারাও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
৫. যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদান করানো হয়, সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শেখার ঐচ্ছিক অপশন চালু করা যেতে পারে। এতে অভিভাবকদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে সন্তানদের পিছিয়ে পড়ার যে শঙ্কা রয়েছে তা দূরীভূত হবে। এছাড়াও অংকের মতো আরো কয়েকটি বই যেগুলো স্থানীয় ভাষায় পাঠ দান করার তেমন কোনো প্রযোজনীয়তা নেই সেগুলো বাংলা ভাষায় পাঠ দান করার ঐচ্ছিক অপশন থাকতে পারে।
৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার সাথে বাংলা ভাষার অভিধান তৈরি করা, তাদের সাহিত্য, সংগীত ও উপ কথাগুলো অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় পুস্তক আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের সাহিত্য সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং এই ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব।
৭. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দ যেগুলো সহজবোধ্য, শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় সেগুলো বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করা যেতে পারে।
৮. প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ রেকর্ড করে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করা।
৯. সমতলের বাংলাভাষীদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, সংরক্ষণ ও গবেষণায় উৎসাহিত করা যেতে পারে। কারণ এ সকল ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল ওই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালির দায়িত্ব বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জাতি গোষ্ঠীগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা।
১০. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভাষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প, উচ্চতর গবেষণা চালু করা যেতে পারে।
১১. এনসিটিবি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিউটের কাজে সংযোগ ও সমন্বয় করা গেলে এক্ষেত্রে অধিক ভাল ফল আশা করা যেতে পারে।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহ আমাদের সম্পদ। নাগরিক হিসেবে আমাদের জাতীয় দায়িত্ব তাদের সুন্দর, নিরাপদ ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা করা। এক্ষেত্রে তাদের ভাষার ভূমিকা যেমন অপরিসীম, তেমনি ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।
♦ লেখক: সম্পাদক, পার্বত্যনিউজ, কম ও চেয়ারম্যান, সিএইচটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন।